এই অধ্যায়ে আমরা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর [ The Famine of 1770 ] নিয়ে আলোচনা করব।
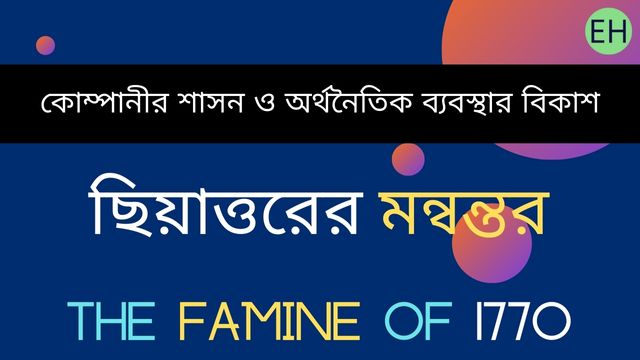
ভারত কৃষি-প্রধান দেশ এবং ভারতের কৃষি ব্যবস্থা বহুলাংশে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে ভারতে বহুবার বহু মারাত্মক ধরনের দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছে। মোগল আমলেও ভারতে দুর্ভিক্ষের পরিমাণ নেহাৎ কম ছিল না। বাংলায় দ্বৈত শাসনের কালে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ইংরেজী ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। স্থায়িত্ব, ব্যাপকতা ও ভয়াবহতার দিক থেকে এই দুর্ভিক্ষ নজিরবিহীন। বাংলা ১১৭৬ সালে সংঘটিত হওয়ার জন্য এই দুর্ভিক্ষ ‘ছিয়াত্তরের মন্বন্তর’ নামে পরিচিত। মন্বন্তর কথার অর্থ ‘দুর্ভিক্ষ’ বা ‘আকাল’।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ :
অনাবৃষ্টি-জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হলেও মনুষ্য-সৃষ্ট নানা কারণও এর সঙ্গে জড়িত ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীদের সীমাহীন লোভ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এই দুর্ভিক্ষকে ভয়ঙ্কর করে তোলে।
(১) প্রাকৃতিক কারণ :
কৃষি-প্রধান দেশ ভারতে কৃষি মূলত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ হল প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অনাবৃষ্টি। ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে বৃষ্টিপাতের অভাবে ভাল ফসল হয়নি। পরের বছর—১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে একফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। এই ব্যাপক অনাবৃষ্টির ফলে মাঠ-ঘাট- পুকুর সব শুকিয়ে গিয়ে বাংলায় এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ সময় আবার বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে থাকে, যার ফলে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায় এবং বিভিন্ন গ্রামে যে সামান্য পরিমাণ চাল মজুত ছিল, তাও নষ্ট হয়। সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন-এর ‘সিয়ার-উল্- মুতাক্ষরিণ’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৭৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে দুর্ভিক্ষ ও বসন্তরোগে বহু গ্রাম উজাড় হয়ে যায়।
(২) রাজস্বের হার বৃদ্ধি :
দুর্ভিক্ষের জন্য দ্বৈত শাসনব্যবস্থাও যথেষ্ট দায়ী ছিল। দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানীর ভূমি-রাজস্ব নীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধিক হারে রাজস্ব আদায়। প্রজার সুবিধা-অসুবিধা, কৃষকের স্বার্থ, উৎপাদনের ঘাটতি প্রভৃতি বিবেচনা না করে তারা কেবল অধিক রাজস্ব আদায়ের দিকেই নজর দিত। অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের জন্য তারা ইজারাদার নিয়োগ করে এবং জমিতে ইজারাদারদের স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন বলে তারা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামতো শোষণ করত। নবাব আলিবর্দির আমলে পূর্ণিয়া জেলা থেকে রাজস্ব হিসেবে আদায় হত বছরে ৪ লক্ষ টাকা, কিন্তু নতুন কর্মচারী সুচেতরাম সেখান থেকে আদায় করতেন ২৫ লক্ষ টাকা। এ ধরনের প্রজা-শোষণ সকল জেলাতেই চলত। মহম্মদ রেজা খাঁ আবার এই বাড়তি করের ওপর ‘নজর’ নামে এক ধরনের কর চাপিয়ে দেন। এর ফলে প্রজার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। কার্টিয়ারের পূর্ববর্তী গভর্নর ভেরেলেস্ট কোম্পানীর কর্তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, “ব্যবসা-বাণিজ্যে যত খুশি লাভ করা যায়, কিন্তু জমির ওপর যত খুশি রাজস্ব আদায় করা যায় না। এক্ষেত্রে জোর-জুলুম চালালে ইংরেজ জাতির চরিত্র কলুষিত হবে।” সেদিন তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। কৃষকদের পক্ষে বাড়তি রাজস্ব দেবার ক্ষমতা না থাকায় অনেকেই কৃষিকার্য পরিত্যাগ করে পলায়ন করে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায়।
(৩) প্রশাসনিক দুর্বলতা ও ব্যক্তিগত বাণিজ্য :
কোম্পানীর প্রশাসনিক দুর্বলতা ও কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকেও দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা যায়। কোম্পানী বাংলাদেশে দেওয়ানীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, কিন্তু কোন প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। প্রশাসন ছিল ক্ষমতাহীন অপদার্থ নবাবের হাতে। কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যথেচ্ছ হারে রাজস্ব আদায় করা—বাংলার মানুষের সুখ-দুঃখের দিকে নজর রাখা নয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে কোম্পানীর কর্মচারী, দালাল ও গোমস্তারা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামতো শোষণ করত, ব্যক্তিগত বাণিজ্য চালাত, উৎপাদককে স্বল্পমূল্যে দ্রব্য বিক্রয় এবং ক্রেতাকে বেশি মূল্যে দ্রব্য ক্রয়ে বাধ্য করত। এর ফলাফল দেশের পক্ষে ভাল হয়নি।
(৪) চালের দাম বৃদ্ধি এবং কোম্পানীর মজুতদারী :
ব্যাপক শস্যহানির ফলে চালের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এযুগে সাধারণ অবস্থায় চালের দাম ছিল পাঁচ-ছ’ আনা মণ (চল্লিশ সের)। কিন্তু ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে খোদ মুর্শিদাবাদে চালের দাম ওঠে টাকায় ছয় বা সাত সের। শহর মুর্শিদাবাদে এই অবস্থা হলে গ্রাম বাংলার চিত্র কি তা সহজেই অনুমেয়। খাদ্যের জন্য সারা দেশে হাহাকার পড়ে যায়। এ সময় কোম্পানীর স্বার্থান্ধ নীতি সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে। ফসলহানির খবর পেয়েই কোম্পানী তার সেনাবাহিনী, ইওরোপীয় অধিবাসী ও কলকাতার মানুষদের জন্য চাল মজুত করে ফেলে। একটি সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, কোম্পানী এ সময় ১,২০,০০০ মণ চাল মজুত করেছিল। কোম্পানীর সেনাবাহিনীর জন্য শুধুমাত্র কলকাতাতেই মজুত ছিল ৬০,০০০ মণ চাল। এ সময় কোম্পানী মাদ্রাজের সেনাবাহিনীর জন্যও জাহাজে করে চাল পাঠায়। চালের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীরাও ধান-চালের ব্যবসায় মেতে ওঠে। তারা গরিব চাষীদের কাছ থেকে বীজধান পর্যন্ত কিনে নেয়। বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে যায়। ইয়ং-হাজব্যান্ড নামক জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এই দুর্ভিক্ষের জন্য মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের চাল গুদামজাত করার ঘটনাকে দায়ী করেছেন। তিনি লেখেন যে, “দেশে যা কিছু খাদ্য ছিল তা ইংরেজ বণিকদের একচেটিয়া দখলে চলে গেল। খাদ্যের পরিমাণ যত কমতে লাগল ততই দাম বাড়তে লাগল।” র্যামসে ম্যুর বলেন যে, “জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধির জন্য দায়ী ছিল কঠোরভাবে রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা ও তাদের জীবনধারণের পণ্য-সামগ্রী নিয়ে ব্যবসায়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের সীমাহীন লাভের আকাঙ্ক্ষা।”
(৫) গ্রামীণ ঋণ :
প্রচলিত গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থাও প্রজার দুর্দশা বৃদ্ধি করে। এই ব্যবস্থা অনুসারে বে-মরসুম অর্থাৎ অসুবিধার সময় কৃষক আড়তদারদের কাছ থেকে ধার হিসেবে খাদ্যশস্য পেত, এবং ফসল উঠলে কৃষক তা পরিশোধ করত। অজন্মার দরুন চাষ-বাস বন্ধ হয়ে গেলে আড়তদাররা চাষীদের ধার দেওয়া বন্ধ করে। এর ফলে তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।
(৬) মুদ্রা সংকট :
দেওয়ানী লাভের ফলে কোম্পানী যে-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তাতে প্রজাদের রাজস্ব মেটাতে হত নগদ রৌপ্যমুদ্রায়। সমাজের নিম্নস্তরে মুদ্রার প্রচলন ছিল না বললেই হয়। তাই রাজস্ব মেটাবার জন্য কৃষক তার শস্য বিক্রি করতে বাধ্য হত এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীরা তা সস্তায় কিনে যথেষ্ট মুনাফা লুটত। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র চাষীর পক্ষে শস্য কেনা সম্ভব ছিল না, কারণ তার হাতে রৌপ্যমুদ্রা ছিল না। মুদ্রা সঙ্কটের ফলে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, যার পরিণতি হল অর্থনৈতিক মন্দা।
(৭) স্বতন্ত্র খাদ্য-অঞ্চল :
সরকার এ সময় সমগ্র বাংলা সুবাকে কয়েকটি খাদ্য-অঞ্চলে বিভক্ত করে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। বাংলা ও বিহার দুটি পৃথক খাদ্য- অঞ্চল ছিল। জেলাগুলিও এক-একটি পৃথক খাদ্য-অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং বাংলা থেকে বিহারে বা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্য শস্যের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। এই অবস্থার সুযোগ নেয় কোম্পানীর কর্মচারী ও তাদের গোমস্তারা। সস্তা দরে কেনা খাদ্যশস্য উচ্চমূল্যে বিক্রি করে তারা প্রচুর মুনাফা লুটতে থাকে। অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তাঁর ‘ওয়েলথ অব নেশনস্’ (‘Wealth of Nations’) গ্রন্থে লিখছেন যে, কয়েক বছর আগে বাংলাদেশে যে খরা গেল তার ফলে বড় রকমের খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার কথা। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা খাদ্য ব্যবসায়ীদের ওপর কতকগুলি অন্যায় নিয়মরীতি এবং অবিবেচনাপ্রসূত বাধানিষেধ আরোপ করার ফলে ঐ খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষে পরিণত হয়।”
মন্বন্তরের ভয়াবহতা :
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপ, তীব্রতা বা ব্যাপকতা বাংলা সুবা-র সর্বত্র সমভাবে অনুভূত হয়নি। পূর্ণিয়া, নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, পাচেট বা রানীগঞ্জ, বর্ধমানের উত্তর তীব্রতা ও পশ্চিম ভাগ, ভাগলপুর, রাজমহল, হুগলী, যশোহর, মালদহ ও চব্বিশ পরগনা ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল। এদের মধ্যে পূর্ণিয়া জেলায় ক্ষয়ক্ষতি ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে বাংলা সুবার এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়। এ সময় বাংলার জনসংখ্যা ছিল তিন কোটি। সব জেলায় মৃত্যুর হার সমান ছিল না—অনেক জেলায় এই হার ছিল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।
উইলিয়ম হান্টার-এর ‘অ্যানাল্ল্স্ অফ রুরাল বেঙ্গল’ গ্রন্থ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দমঠ’ গ্রন্থে এই দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ বর্ণনা আছে। ক্ষুধার জ্বালা ধনী জমিদার ও দরিদ্র প্রজাকে এক করে দেয়। মানুষের দুরবস্থা খাদ্যাভাবে মানুষ প্রথমে গাছের পাতা ও ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করার চেষ্টা করে। পরে তার অভাবে মানুষ শবদেহ থেকে মাংস কেটে খেতে আরম্ভ করে। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ প্রথমে গোরু, বাছুর, লাঙ্গল বিক্রি করতে থাকে, পরে নিজ সন্তানকেও বিক্রি করতে বাধ্য হয়। শেষে অবস্থা এমন হয় যে, বাজারে সকলেই বিক্রি করতে চায়—ক্রেতা কেউ নেই। অনাহার, অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ, কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব, স্তূপীকৃত পচা-গলা কঙ্কালসার মৃতদেহ সমস্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে। গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে যায় এবং অচিরেই তা ব্যাঘ্র ও শ্বাপদ- সঙ্কুল ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়।
অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ :
ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু এবং কৃষকদের দেশত্যাগ সত্ত্বেও কোম্পানীর ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কিন্তু বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি বরং তা বেড়েছিল। দুর্ভিক্ষ হলে সাধারণত খাজনা মকুব করা হয়, কিন্তু বাংলার চেহারা ছিল ভিন্ন। ১৭৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ যখন চরমে, তখন কোম্পানী পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বেশি রাজস্ব আদায় করে। পরের বছর আরও ১৩ লক্ষ টাকা বেশি খাজনা সংগ্ৰহ আদায় করা হয়। আসলে কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল যে-ভাবে হোক রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এজন্য তারা ‘নাজাই’ নামে এক প্রকার কর আদায় করতে থাকে। মৃত ও পলাতক প্রজাদের দেয় করের ঘাটতি পুরণের জন্য জীবিত প্রজাদের কাছ থেকে এই কর আদায় করা হত।
সরকারি ব্যবস্থা :
দুর্ভিক্ষ নিবারণে সরকারি ত্রাণ ব্যবস্থা ছিল খুবই অপ্রতুল। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছিল প্রায় তিন কোটি মানুষ, কিন্তু সরকার থেকে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৪৩ টাকা, যা ছিল সরকারি ব্যবস্থা ‘অমানবিকভাবে অপ্রতুল’ (‘inhumanly inadequate’)। বিভিন্ন জেলায় অবশ্য কিছু প্রাণকেন্দ্র খোলা হয়। রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে সাতটি ত্রাণকেন্দ্র খোলেন। রেজা খাঁ অপেক্ষা বিহারে সিতাব রায়ের ব্যবস্থা আরও উন্নত ছিল। তিনি বেনারস থেকে সস্তায় চাল আনিয়ে ৩০ হাজার টাকার চাল দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করেন।
ফলাফল:
জনসংখ্যা হ্রাস :
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সূচনা করে। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। তখন সুরে বাংলার লোকসংখ্যা ছিল তিন কোটি। সুতরাং এই দুর্ভিক্ষে এক কোটি লোকের প্রাণহানি ঘটে। উইলিয়ম হান্টারের মতে, সুবে বাংলায় শতকরা ৩৬ জন মানুষের মৃত্যু হয়। অনেকের মতে মৃত্যুর হার ছিল পঞ্চাশ শতাংশ। যাই হোক, মৃতের সংখ্যা যে বিপুল ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই।
জনশূন্য গ্রামগুলি জঙ্গলে পরিণত :
ব্যাপক হারে মৃত্যু এবং জীবিত ব্যক্তিদের গ্রাম ত্যাগের ফলে গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়ে। চাষ- বাস, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে যায়। জনশূন্য হয়ে যাওয়ায় গ্রামগুলি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তা অচিরেই হিংস্র জীবজন্তুর লীলাভূমিতে পরিণত হয়। এই বিপর্যয়ের উনিশ বছর বাদে লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে লেখেন যে, বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চল এখন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এবং তা হল হিংস্র জীবজন্তুর আবাসস্থল।
অস্থায়ী রায়তের সংখ্যা বৃদ্ধি :
মন্বন্তরের ফলে কিছুদিনের জন্য বাংলার কৃষি-ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। বাংলার কৃষকদের একটি বিরাট অংশ মারা যাওয়ায় বা দেশত্যাগী হওয়ায় বাংলায় কৃষিকার্যে লোকাভাব দেখা দেয়। অস্থায়ী রায়তের সংখ্যা বৃদ্ধি এতদিন কৃষি-জমির চেয়ে কৃষকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় কৃষক শোষিত হত, কিন্তু মন্বন্তর এই অবস্থাটি পাল্টে দেয়। কৃষকের তুলনায় কৃষি জমির পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে যায়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অস্থায়ী চাষী বা পাইকস্থ রায়তরা জমিদারের কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়। অপরদিকে স্থায়ী রায়ত বা খোদ কস্ত রায়তদের ওপর বেশি রাজস্ব চাপাবার চেষ্টা হলে তারা দেশত্যাগ করে পাইকস্থ রায়ত বা অস্থায়ী রায়তে পরিণত হয়। মন্বন্তরের পরবর্তীকালে পাইকস্থ রায়তের সংখ্যা বৃদ্ধি বাংলার অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
নতুন জমিদার শ্রেণী :
উইলিয়ম হান্টারের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মন্বন্তরের ফলে বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ পুরানো জমিদার বা অভিজাত পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। অনেকে দুর্ভিক্ষে মারা যান। অনেকে কর দিতে না পেরে জমিদারী হারান। এ সময় এই পরিবারগুলি এতই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, গৃহের মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করেও তাঁরা ঋণ মেটাতে সক্ষম হননি। সময়মতো খাজনা দিতে না পারার জন্য বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজারা কারারুদ্ধ হন। খাজনা দিতে না পারার জন্য নাটোরের রানী ভবানী এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য বহু ইজারাদারও ইজারা থেকে বঞ্চিত হন। পুরানো জমিদার ও ইজারাদারদের স্থলে বহু নতুন লোক, যাঁরা কলকাতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও গোমস্তার কাজ করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, তাঁরাই নতুন জমিদার ও ইজারাদার হয়ে বসেন। গ্রাম বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে এইসব নতুন জমিদারদের কোন সম্পর্ক ছিল না। এর ফলাফল বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিতে ভাল হয়নি।
শিল্প :
কেবল কৃষিই নয়—মন্বন্তর শিল্পের ওপরেও বিরাট আঘাত হানে। তাঁতী, কামার, কুমোর এবং অন্যান্য শিল্পী ও কারিগরদের ব্যাপক প্রাণহানির ফলে লবণ, সুতিবস্ত্র, রেশম, সোরা প্রভৃতি শিল্প- বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। মাঝি, গোরুর গাড়ির চালক, মালঙ্গী ও শ্রমিকদের মৃত্যু মাল-পরিবহন ব্যবস্থাকে ঘোরতর সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। মন্বন্তরের পর সুত্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, কিন্তু সে তুলনায় আনুপাতিক হারে সুতিবস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি না ঘটায় বহু তাঁতী শিল্পকর্ম ত্যাগ করে অন্য পেশায় নিযুক্ত হয়। এইসব কারণে উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মানেরও অবনতি ঘটে।
নৈতিক অবক্ষয় ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি :
মন্বন্তরের ফলে পারিবারিক জীবন ভেঙে পড়ে এবং নানা ধরনের সামাজিক কুফল দেখা দেয়। অন্নাভাবে মানুষ নীতিজ্ঞান হারিয়ে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ স্ত্রী-বিক্রয়, সন্তান- বিক্রয় প্রভৃতি অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়। এ সময় আইন-শৃঙ্খলাও ভেঙে পড়ে এবং চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি বৃদ্ধি পায়। গ্রামের পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানসমূহ চোর-ডাকাতদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। এ সময় উত্তর ভারত থেকে আগত ডাকাতের দল সন্ন্যাসী ও ফকিরের ছদ্মবেশে উত্তরবঙ্গে ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়। বহুক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদাররাও এইসব লুঠেরা-দস্যুদের সঙ্গে যোগদান করে ।
দ্বৈত শাসনের অবসান :
১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের ফলে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, ‘দ্বৈত শাসন’ নামক উদ্ভট শাসনব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে নিজ হস্তে বাংলার শাসনভার গ্রহণের পক্ষে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই মর্মে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ গভর্নর হিসেবে ভারতে আসেন • বং দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানীর পক্ষে সকল ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।
বিষয় -সংক্ষেপ
- ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার- উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করে। তারা কিন্তু দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নিজেরা সরাসরি গ্রহণ করে। এর পরিবর্তে তারা এক অদ্ভুত ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যার নাম দ্বৈত শাসন’। এই শাসনে জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৭৭১ খ্রি ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তন করে।
- কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বা ‘প্রাইভেট ট্রেড’ হল এ যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন ছিল খুবই কম। তাই কোম্পানী এদেশে তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য অনুমোদন করেছিল। এইভাবে অবৈধ পথে তারা বিপুল অর্থ রোজগার করত। তাদের অনাচার ও দুর্নীতির ফলে দেশে এমনই অরাজকতা ও যথেচ্ছাচার দেখা দেয় যে, কোম্পানী আইন করে এই ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়।
- ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ব্যাপক স্থানে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর একটি প্রধান কারণ হলেও কোম্পানীর অপদার্থতাও এই দুর্ভিক্ষের জন্য বহুলাংশে দায়ী। দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও জনজীবনে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে।